রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
লিপিকা
[‘লিপিকা’র গল্পগুলোকে কবি নিজেই ‘কথিকা’ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন । রবীন্দ্রসাহিত্যে ভিন্নধারার এই গল্পগুলো এক অনন্য সম্পদ। বাংলাসাহিত্যের গল্পের ধারাবদলে ‘লিপিকা’ একটি মাইলফলক। ১৯২২সালে প্রকাশিত হয় ‘লিপিকা’। এই ‘কথিকা’ গুলি লেখার সময় তিনি নানা কারণে কিছুটা অবসাদগ্রস্ত ছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে চেয়েও কাউকে পাশে পাচ্ছিলেন না। একলাই চলতে হয়েছিল তাঁকে। অবলীলায় ত্যাগ করেছিলেন ইংরেজদের দেওয়া ‘নাইটহুড’। এমনই মানসিক টানাপোড়েনের সঙ্গে জুড়ে ছিল তাঁর কবিমন আর কর্মিমনের এক চিরকালীন দ্বন্দ্ব। কাজের জন্য একটা অন্য জীবন চেয়েছিলেন কবি। যাপিত জীবন যেন তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারছিল না। এ দ্বন্দ্ব তাঁর মননে চিরস্থায়ী হয়েছিল। পুনর্পাঠে আজ পড়ুন বিশ্বকবির লিপিকা’র কিছু গল্প।- সম্পাদক]
একটি চাউনি
গাড়িতে ওঠবার সময় একটুখানি মুখ ফিরিয়ে সে আমাকে তার শেষ চাউনিটি দিয়ে গেছে।
এই মস্ত সংসারে ঐটুকুকে আমি রাখি কোন্খানে।
দণ্ড পল মুহূর্ত অহরহ পা ফেলবে না, এমন একটু জায়গা আমি পাই কোথায়।
মেঘের সকল সোনার রঙ যে সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায় এই চাউনি কি সেই সন্ধ্যায় মিলিয়ে যাবে। নাগকেশরের সকল সোনালি রেণু যে বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় এও কি সেই বৃষ্টিতেই ধুয়ে যাবে।
সংসারের হাজার জিনিসের মাঝখানে ছড়িয়ে থাকলে এ থাকবে কেন— হাজার কথার আবর্জনায়, হাজার বেদনার স্তূপে।
তার ঐ এক চকিতের দান সংসারের আর-সমস্তকে ছাড়িয়ে আমারই হাতে এসে পৌঁচেছে। একে আমি রাখব গানে গেঁথে ছন্দে বেঁধে; আমি একে রাখব সৌন্দর্যের অমরাবতীতে।
পৃথিবীতে রাজার প্রতাপ, ধনীর ঐশ্বর্য হয়েছে মরবারই জন্যে। কিন্তু, চোখের জলে কি সেই অমৃত নেই যাতে এই নিমেষের চাউনিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে।
গানের সুর বললে, “আচ্ছা, আমাকে দাও। আমি রাজার প্রতাপকে স্পর্শ করি নে, ধনীর ঐশ্বর্যকেও না, কিন্তু ঐ ছোটো জিনিসগুলিই আমার চিরদিনের ধন; ঐগুলি দিয়েই আমি অসীমের গলার হার গাঁথি।”
একটি দিন
মনে পড়ছে সেই দুপুরবেলাটি। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারা ক্লান্ত হয়ে আসে, আবার দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।
ঘরে অন্ধকার, কাজে মন যায় না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের সুর লাগালেম।
পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল দুয়ার পর্যন্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নিচু করে সেলাই করতে লাগল। তার পরে সেলাই বন্ধ করে জানলার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।
বৃষ্টি ধরে এল, আমার গান থামল। সে উঠে চুল বাঁধতে গেল।
এইটুকু ছাড়া আর কিছুই না। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই একটি দুপুরবেলা।
ইতিহাসে রাজাবাদশার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, সস্তা হয়ে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু একটি দুপুরবেলার ছোটো একটু কথার টুকরো দুর্লভ রত্নের মতো কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল, দুটি লোক তার খবর জানে।
পায়ে চলার পথ
১
এই তো পায়ে চলার পথ।
এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, খেয়াঘাটের পাশে বটগাছতলায়। তার পরে ও পারের ভাঙা ঘাট থেকে বেঁকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে; তার পরে তিসির খেতের ধার দিয়ে, আমবাগানের ছায়া দিয়ে, পদ্মদিঘির পাড় দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পৌঁচেছে জানি নে।
এই পথে কত মানুষ কেউ-বা আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে, কেউ-বা সঙ্গ নিয়েছে, কাউকে-বা দূর থেকে দেখা গেল; কারও-বা ঘোমটা আছে, কারও-বা নেই; কেউ-বা জল ভরতে চলেছে, কেউ বা জল নিয়ে ফিরে এল।
২
এখন দিন গিয়েছে, অন্ধকার হয়ে আসে।
একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ একান্তই আমার; এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।
নেবুতলা উজিয়ে সেই পুকুরপাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়ালবাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে—সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটিবারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না, “এই যে! ” এ পধ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়।
আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম; দেখলুম, এই পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।
যত কাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটিমাত্র ধূলিরেখায় সংক্ষিপ্ত করে এঁকেছে; সেই একটি রেখা চলেছে সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্তের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আর-এক সোনার সিংহদ্বারে।
৩
“ওগো পায়ে চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার ধূলিবন্ধনে বেঁধে নীরব করে রেখো না। আমি তোমার ধুলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে কানে বলো।”
পথ নিশীথের কালো পর্দার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে চুপ করে থাকে।
“ওগো পায়ে চলার পথ, এত পথিকের এত ভাবনা, এত ইচ্ছা, সে-সব গেল কোথায়।”
বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্ত অবধি ইশারা মেলে রাখে।
“ওগো পায়ে চলার পথ, তোমার বুকের উপর যে-সমস্ত চরণপাত একদিন পুষ্পবৃষ্টির মতো পড়েছিল আজ তারা কি কোথাও নেই।”
পথ কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁছল, যেখানে তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব।
পুরোনো বাড়ি
১
অনেক কালের ধনী গরিব হয়ে গেছে, তাদেরই ঐ বাড়ি।
দিনে দিনে ওর উপরে দুঃসময়ের আঁচড় পড়ছে।
দেয়াল থেকে বালি খসে পড়ে, ভাঙা মেঝে নখ দিয়ে খুঁড়ে চড়ুইপাখি ধুলোয় পাখা ঝাপট দেয়, চণ্ডীমণ্ডপে পায়রাগুলো বাদলের ছিন্ন মেঘের মতো দল বাঁধল।
উত্তর দিকের এক-পাল্লা দরজা কবে ভেঙে পড়েছে কেউ খবর নিলে না। বাকি দরজাটা, শোকাতুরা বিধবার মতো, বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খেয়ে পড়ে—কেউ তাকিয়ে দেখে না।
তিন মহল বাড়ি। কেবল পাঁচটি ঘরে মানুষের বাস, বাকি সব বন্ধ। যেন পঁচাশি বছরের বুড়ো, তার জীবনের সবখানি জুড়ে সেকালের কুলুপ-লাগানো স্মৃতি, কেবল একখানিতে একালের চলাচল।
বালি-ধসা ইঁট-বের-করা বাড়িটা তালি-দেওয়া-কাঁথা-পরা উদাসীন পাগলার মতো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে; আপনাকেও দেখে না, অন্যকেও না।
২
একদিন ভোররাত্রে ঐ দিকে মেয়ের গলায় কান্না উঠল। শুনি, বাড়ির যেটি শেষ ছেলে, শখের যাত্রায় রাধিকা সেজে যার দিন চলত, সে আজ আঠারো বছরে মারা গেল।
কদিন মেয়েরা কাঁদল, তার পরে তাদের আর খবর নেই।
তার পরে সকল দরজাতেই তালা পড়ল।
কেবল উত্তর দিকের সেই একখানা অনাথা দরজা ভাঙেও না, বন্ধও হয় না; ব্যথিত হৃৎপিণ্ডের মতো বাতাসে ধড়াস ধড়াস করে আছাড় খায়।
৩
একদিন সেই বাড়িতে বিকেলে ছেলেদের গোলমাল শোনা গেল।
দেখি, বারান্দা থেকে লালপেড়ে শাড়ি ঝুলছে।
অনেক দিন পরে বাড়ির এক অংশে ভাড়াটে এসেছে। তার মাইনে অল্প, ছেলে-মেয়ে বিস্তর। শ্রান্ত মা বিরক্ত হয়ে তাদের মারে, তারা মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে।
একটা আধাবয়সী দাসী সমস্ত দিন খাটে, আর গৃহিণীর সঙ্গে ঝগড়া করে; বলে ‘চললুম’, কিন্তু যায় না।
৪
বাড়ির এই ভাগটায় রোজ একটু-আধটু মেরামত চলছে।
ফাটা সাসির উপর কাগজ আঁটা হল; বারান্দায় রেলিঙের ফাঁকগুলোতে বাঁখারি বেঁধে দিলে শোবার ঘরে ভাঙা জানলা ইঁট দিয়ে ঠেকিয়ে রাখলে; দেয়ালে চুনকাম হল, কিন্তু কালো ছাপগুলোর আভাস ঢাকা পড়ল না।
ছাদে আলসের ’পরে গামলায় একটা রোগা পাতাবাহারের গাছ হঠাৎ দেখা দিয়ে আকাশের কাছে লজ্জা পেলে। তার পাশেই ভিত ভেদ করে অশথ গাছটি সিধে দাঁড়িয়ে; তার পাতাগুলো এদের দেখে যেন খিল্খিল্ করে হাসতে লাগল।
মস্ত ধনের মস্ত দারিদ্র্য। তাকে ছোটো হাতের ছোটো কৌশলে ঢাকা দিতে গিয়ে তার আবরু গেল।
কেবল উত্তর দিকের উজাড় ঘরটির দিকে কেউ তাকায় নি। তার সেই জোড়ভাঙা দরজা আজও কেবল বাতাসে আছড়ে পড়ছে, হতভাগার বুক-চাপড়ানির মতো।
প্রথম চিঠি
১
বধূর সঙ্গে তার প্রথম মিলন, আর তার পরেই সে এই প্রথম এসেছে প্রবাসে।
চলে যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে কান্নাটি ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে চকিতে ওর চোখে পড়ল।
মন বললে, ‘ফিরি, দুটো কথা বলে আসি।’
কিন্তু, সেটুকু সময় ছিল না।
সে দূরে আসবে বলে একজনের দুটি চোখ বয়ে জল পড়ে, তার জীবনে এমন সে আর-কখনো দেখে নি।
পথে চলবার সময় তার কাছে পড়ন্ত রোদ্দুরে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম ব্যথার ভাণ্ডারে তার মতো একটি মানুষেরও নিমন্ত্রণ আছে, এই কথা মনে করে বিস্ময়ে তার বুক ভরে উঠল।
যেখানে সে কাজ করতে এসেছে সে পাহাড়। সেখানে দেবদারুর ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মতো পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোটো ছোটো ঝরনা কাকে যেন আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায় লুকিয়ে-চুরিয়ে।
আয়নার মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাসী সেই ছবিরই আভাস দেখে, নববধূর গোপন ব্যাকুলতার ছবি।
২
আজ দেশ থেকে তার স্ত্রীর প্রথম চিঠি এল।
লিখেছে, “তুমি কবে ফিরে আসবে। এসো এসো, শীঘ্র এসো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।”
এই আসা-যাওয়ার সংসারে তারও চলে যাওয়া আর তারও ফিরে আসার যে এত দাম ছিল, এ কথা কে জানত। সেই দুটি আতুর চোখের চাউনির সামনে সে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখলে, আর তার মন বিস্ময়ে ভরে উঠল।
ভোরেবেলায় উঠে চিঠিখানি নিয়ে দেবদারুর ছায়ায় সেই বাঁকা পথে সে বেড়াতে বেরোল। চিঠির পরশ তার হাতে লাগে আর কানে যেন সে শুনতে পায়, “তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কান্নায় ভেসে গেল।”
মনে মনে ভাবতে লাগল, ‘এত কান্নার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে।’
৩
এমন সময় সূর্য উঠল পূর্ব দিকের নীল পাহাড়ের শিখরে। দেবদারুর শিশিরভেজা পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো ঝিল্মিল্ করে উঠল।
হঠাৎ চারটি বিদেশিনী মেয়ে দুই কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তার বাঁকের মুখে তার সামনে এসে পড়ল। কী জানি কী ছিল তার মুখে, কিংবা তার সাজে, কিম্বা তার চালচলনে—বড়ো মেয়েদুটি কৌতুকে মুখ একটুখানি বাঁকিয়ে চলে গেল। ছোটো মেয়েদুটি হাসি চাপবার চেষ্টা করলে, চাপতে পারলে না; দুজনে দুজনকে ঠেলাঠেলি করে খিল্খিল্ করে হেসে ছুটে গেল।
কঠিন কৌতুকের হাসিতে ঝরনাগুলিরও সুর ফিরে গেল। তারা হাততালি দিয়ে উঠল। প্রবাসী মাথা হেঁট করে চলে আর ভাবে, ‘আমার দেখার মূল্য কি এই হাসি।’
সেদিন রাস্তায় চলা তার আর হল না। বাসায় ফিরে গেল, একলা ঘরে বসে চিঠিখানি খুলে পড়লে, “তুমি কবে ফিরে আসবে। এসো, এসো, শীঘ্র এসো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।
প্রথম শোক
বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা।
সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, “আমাকে চিনতে পার না? ”
আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম। বললেম, “মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নে।”
সে বললে, “আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।”
তার চোখের কোণে একটু ছলছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।
অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বললেম, “সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেছ।”
কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাসলে; বুঝলেম, সবটুকু রয়ে গেছে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েছে।
আমি জিজ্ঞাসা করলেম, “আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজও তোমার কাছে রেখে দিয়েছ।”
সে বললে, “এই দেখো-না আমার গলার হার।”
দেখলেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও খসে নি।
আমি বললেম, “আমার আর তো সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও তো ম্লান হয় নি।”
আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বললে, “মনে আছে? সেদিন বলেছিলে, তুমি সান্ত্বনা চাও না, তুমি শোককেই চাও।”
লজ্জিত হয়ে বললেম, “বলেছিলেম। কিন্তু, তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভুলে গেলেম।”
সে বললে, “যে অর্ন্তযামীর বর, তিনি তো ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও।”
আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, “এ কী তোমার অপরূপ মূর্তি।”
সে বললে, “যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।”
ভুল স্বর্গ
১
লোকটি নেহাত বেকার ছিল।
তার কোনো কাজ ছিল না, কেবল শখ ছিল নানা রকমের।
ছোটো ছোটো কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপরে সে ছোটো ঝিনুক সাজাত। দূর থেকে দেখে মনে হত যেন একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাখির ঝাঁক; কিংবা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, সেখানে গোরু চরছে; কিংবা উঁচুনিচু পাহাড়, তার গা দিয়ে ওটা বুঝি ঝরনা হবে, কিংবা পায়ে-চলা পথ।
বাড়ির লোকের কাছে তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে পণ করত পাগলামি ছেড়ে দেবে, কিন্তু পাগলামি তাকে ছাড়ত না।
২
কোনো কোনো ছেলে আছে সারা বছর পড়ায় ফাঁকি দেয়, অথচ পরীক্ষায় খামকা পাশ করে ফেলে। এর সেই দশা হল।
সমস্ত জীবনটা অকাজে গেল, অথচ মৃত্যুর পরে খবর পেলে যে, তার স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর।
কিন্তু, নিয়তি স্বর্গের পথেও মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না। দূতগুলো মার্কা ভুল করে তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এল।
এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই।
এখানে পুরুষরা বলছে, “হাঁফ ছাড়বার সময় কোথা।” মেয়েরা বলছে, “চললুম, ভাই, কাজ রয়েছে পড়ে।” সবাই বলে, “সময়ের মূল্য আছে।” কেউ বলে না, “সময় অমূল্য।” “আর তো পারা যায় না” ব’লে সবাই আক্ষেপ করে, আর ভারি খুশি হয়। “খেটে খেটে হয়রান হলুম” এই নালিশটাই সেখানকার সংগীত।
এ বেচারা কোথাও ফাঁক পায় না, কোথাও খাপ খায় না। রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে চলে, তাতে ব্যস্ত লোকের পথ আটক করে। চাদরটি পেতে যেখানেই আরাম ক’রে বসতে চায়, শুনতে পায়, সেখানেই ফসলের খেত, বীজ পোঁতা হয়ে গেছে। কেবলই উঠে যেতে হয়, সরে যেতে হয়।
৩
ভারি এক ব্যস্ত মেয়ে স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল নিতে আসে।
পথের উপর দিয়ে সে চলে যায় যেন সেতারের দ্রুত তালের গতের মতো।
তাড়াতাড়ি সে এলো-খোঁপা বেঁধে নিয়েছে। তবু দু-চারটে দুরন্ত অলক কপালের উপর ঝুঁকে প’ড়ে তার চোখের কালো তারা দেখবে ব’লে উঁকি মারছে।
স্বর্গীয় বেকার মানুষটি এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, চঞ্চল ঝরনার ধারে তমালগাছটির মতো স্থির।
জানলা থেকে ভিক্ষুককে দেখে রাজকন্যার যেমন দয়া হয়, এঁকে দেখে মেয়েটির তেমনি দয়া হল।
“আহা, তোমার হাতে বুঝি কাজ নেই? ”
নিশ্বাস ছেড়ে বেকার বললে, “কাজ করব তার সময় নেই।”
মেয়েটি ওর কথা কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে, “আমার হাত থেকে কিছু কাজ নিতে চাও? ”
বেকার বললে, “তোমার হাত থেকেই কাজ নেব ব’লে দাঁড়িয়ে আছি।”
“কী কাজ দেব।”
“তুমি যে ঘড়া কাঁখে জল তুলে নিয়ে যাও তারই একটি যদি আমাকে দিতে পার।”
“ঘড়া নিয়ে কী হবে। জল তুলবে? ”
“না, আমি তার গায়ে চিত্র করব।”
মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বললে, “আমার সময় নেই, আমি চললুম।”
কিন্তু বেকার লোকের সঙ্গে কাজের লোক পারবে কেন। রোজ ওদের উৎসতলায় দেখা হয় আর রোজ সেই একই কথা, “তোমার কাঁখের একটি ঘড়া দাও, তাতে চিত্র করব।”
হার মানতে হল, ঘড়া দিলে।
সেইটিকে ঘিরে ঘিরে বেকার আঁকতে লাগল কত রঙের পাক, কত রেখার ঘর।
আঁকা শেষ হলে মেয়েটি ঘড়া তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। ভুরু বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, “এর মানে? ”
বেকার লোকটি বললে, “এর কোনো মানে নেই।”
ঘড়া নিয়ে মেয়েটি বাড়ি গেল।
সবার চোখের আড়ালে বসে সেটিকে সে নানা আলোতে নানা রকমে হেলিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। রাত্রে থেকে থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে দীপ জ্বেলে চুপ করে বসে সেই চিত্রটা দেখতে লাগল। তার বয়সে এই সে প্রথম এমন কিছু দেখেছে যার কোনো মানে নেই।
তার পরদিন যখন সে উৎসতলায় এল তখন তার দুটি পায়ের ব্যস্ততায় একটু যেন বাধা পড়েছে। পা দুটি যেন চলতে চলতে আন্মনা হয়ে ভাবছে— যা ভাবছে তার কোনো মানে নেই।
সেদিনও বেকার মানুষ এক পাশে দাঁড়িয়ে।
মেয়েটি বললে, “কী চাও।”
সে বললে, “তোমার হাত থেকে আরো কাজ চাই।”
“কী কাজ দেব।”
“যদি রাজি হও, রঙিন সুতো বুনে বুনে তোমার বেণী বাঁধবার দড়ি তৈরি করে দেব।”
“কী হবে।”
“কিছুই হবে না।”
নানা রঙের নানা-কাজ-করা দড়ি তৈরি হল। এখন থেকে আয়না হাতে নিয়ে বেণী বাঁধতে মেয়ের অনেক সময় লাগে। কাজ পড়ে থাকে, বেলা বয়ে যায়।
৪
এ দিকে দেখতে দেখতে কেজো স্বর্গে কাজের মধ্যে বড়ো বড়ো ফাঁক পড়তে লাগল। কান্নায় আর গানে সেই ফাঁক ভরে উঠল।
স্বর্গীয় প্রবীণেরা বড়ো চিন্তিত হল। সভা ডাকলে। তারা বললে, “এখানকার ইতিহাসে কখনো এমন ঘটে নি।”
স্বর্গের দূত এসে অপরাধ স্বীকার করলে। সে বললে, “আমি ভুল লোককে ভুল স্বর্গে এনেছি।”
ভুল লোকটিকে সভায় আনা হল। তার রঙিন পাগড়ি আর কোমরবন্ধের বাহার দেখেই সবাই বুঝলে, বিষম ভুল হয়েছে।
সভাপতি তাকে বললে, “তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে।”
সে তার রঙের ঝুলি আর তুলি কোমরে বেঁধে হাঁফ ছেড়ে বললে, “তবে চললুম।”
মেয়েটি এসে বললে “আমিও যাব।”
প্রবীণ সভাপতি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই সে প্রথম দেখলে এমন-একটা কাণ্ড যার কোনো মানে নেই।
মেঘলা দিনে
রোজই থাকে সমস্তদিন কাজ, আর চার দিকে লোকজন। রোজই মনে হয়, সেদিনকার কাজে, সেদিনকার আলাপে সেদিনকার সব কথা দিনের শেষে বুঝি একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়। ভিতরে কোন্ কথাটি যে বাকি রয়ে গেল তা বুঝে নেবার সময় পাওয়া যায় না।
আজ সকালবেলা মেঘের স্তবকে স্তবকে আকাশের বুক ভেরে উঠেছে। আজও সমস্তদিনের কাজ আছে সামনে, আর লোক আছে চার দিকে। কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে, ভিতরে যা-কিছু আছে বাইরে তা সমস্ত শেষ করে দেওয়া যায় না।
মানুষ সমুদ্র পার হল, পর্বত ডিঙিয়ে গেল, পাতালপুরীতে সিঁধ কেটে মণিমানিক চুরি করে আনলে, কিন্তু একজনের অন্তরের কথা আর-একজনকে চুকিয়ে দিয়ে ফেলা, এ কিছুতেই পারলে না।
আজ মেঘলা দিনের সকালে সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপটে মরছে। ভিতরের মানুষ বলছে, “আমার চিরদিনের সেই আর-একজনটি কোথায়, যে আমার হৃদয়ের শ্রাবণমেঘকে ফতুর করে তার সকল বৃষ্টি কেড়ে নেবে! ”
আজ মেঘলা দিনের সকালে শুনতে পাচ্ছি, সেই ভিতরের কথাটা কেবলই বন্ধ দরজার শিকল নাড়ছে। ভাবছি, “কী করি। কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এখনই আমার বাণী সুরের প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে। কে আছে যার চোখের একটি ইশারায় আমার সব ছড়ানো ব্যথা এক মুহূর্তে এক আনন্দে গাঁথা হবে, এক আলোতে জ্বলে উঠবে। আমার কাছে ঠিক সুরটি লাগিয়ে চাইতে পারে যে আমি তাকেই কেবল দিতে পারি। সেই আমার সর্বনেশে ভিখারি রাস্তার কোন্ মোড়ে।”
আমার ভিতরমহলের ব্যথা আজ গেরুয়াবসন পরেছে। পথে বাহির হতে চায়, সকল কাজের বাহিরের পথে, যে পথ একটিমাত্র সরল তারের একতারার মতো, কোন্ মনের মানুষের চলায় চলায় বাজছে।
সন্ধ্যা ও প্রভাত
এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল।
অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোন্খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।
জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।
এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।
ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পুবের দিকে মুখ করে চলেছে; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফুরোয় নি; ওদের জন্যে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে; রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে, “তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত।”
ওদের হৃৎপিণ্ডের রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।
এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হল।
পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্তা; সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি করছে; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।
সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।
সুয়োরানীর সাধ
সুয়োরানীর বুঝি মরণকাল এল।
তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে, তার কিছুই ভালো লাগছে না। বদ্দি বড়ি নিয়ে এল। মধু দিয়ে মেড়ে বললে, “খাও।” সে ঠেলে ফেলে দিলে।
রাজার কানে খবর গেল। রাজা তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে এল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার কী হয়েছে, কী চাই।”
সে গুমরে উঠে বললে, “তোমরা সবাই যাও; একবার আমার স্যাঙাৎনিকে ডেকে দাও।”
স্যাঙাৎনি এল। রানী তার হাত ধরে বললে, “সই, বসো। কথা আছে।”
স্যাঙাৎনি বললে, “প্রকাশ করে বলো।”
সুয়োরানী বললে, “আমার সাতমহলা বাড়ির এক ধারে তিনটে মহল ছিল দুয়োরানীর। তার পরে হল দুটো, তার পরে হল একটা। তার পরে রাজবাড়ি থেকে সে বের হয়ে গেল।
তার পরে দুয়োরানীর কথা আমার মনেই রইল না।
তার পরে একদিন দোলযাত্রা। নাটমন্দিরে যাচ্ছি ময়ূরপংখি চ’ড়ে। আগে লোক, পিছে লশ্কর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ।
এমন সময় পথের পাশে, নদীর ধারে, ঘাটের উপরটিতে দেখি একখানি কুঁড়েঘর, চাঁপাগাছের ছায়ায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতার ফুল ফুটেছে, দুয়োরের সামনে চালের গুঁড়ো দিয়ে শঙ্খচক্রের আলপনা। আমার ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, ‘আহা, ঘরখানি কার।’ সে বললে, দুয়োরানীর।
তার পরে ঘরে ফিরে এসে সন্ধ্যার সময় বসে আছি, ঘরে প্রদীপ জ্বালি নি, মুখে কথা নেই।
রাজা এসে বললে, ‘তোমার কী হয়েছে, কী চাই।’
আমি বললেম, ‘এ ঘরে আমি থাকব না।’
রাজা বললে, ‘আমি তোমার কোঠাবাড়ি বানিয়ে দেব গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে। শঙ্খের গুঁড়োয় মেঝেটি হবে দুধের ফেনার মতো সাদা, মুক্তোর ঝিনুক দিয়ে তার কিনারে এঁকে দেব পদ্মের মালা।’
আমি বললেম, ‘আমার বড়ো সাধ গিয়েছে, কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকি তোমার বাহিরবাগানের একটি ধারে।’
রাজা বললে, ‘আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।’
কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলে। সে ঘর যেন তুলে-আনা বনফুল। যেমনি তৈরি হল অমনি যেন মুষড়ে গেল। বাস করতে গেলেম, কেবল লজ্জা পেলেম।
তার পরে একদিন স্নানযাত্রা।
নদীতে নাইতে গেছি। সঙ্গে একশো সাত জন সঙ্গিনী। জলের মধ্যে পাল্কি নামিয়ে দিলে, স্নান হল।
পথে ফিরে আসছি, পাল্কির দরজা একটু ফাঁক করে দেখি, ও কোন্ ঘরের বউ গা। যেন নির্মাল্যের ফুল। হাতে সাদা শাঁখা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। সনানের পর ঘড়ায় ক’রে জল তুলে আনছে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ার উপর ঝিকিয়ে উঠছে।
ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, ‘মেয়েটি কে, কোন্ দেবমন্দিরে তপস্যা করে।’
ছত্রধারিণী হেসে বললে, ‘চিনতে পারলে না? ঐ তো দুয়োরানী।’
তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই। রাজা এসে বললে, ‘তোমার কী হয়েছে, কী চাই।’
আমি বললেম, ‘আমার বড়ো সাধ, রোজ সকালে নদীতে নেয়ে মাটির ঘড়ায় জল তুলে আনব বকুলতলার রাস্তা দিয়ে।’
রাজা বললে, ‘আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।’
রাস্তায় রাস্তায় পাহারা বসল, লোকজন গেল সরে।
সাদা শাঁখা পরলেম আর লালপেড়ে শাড়ি। নদীতে স্নান সেরে ঘড়ায় করে জল তুলে আনলেম। দুয়োরের কাছে এসে মনের দুঃখে ঘড়া আছড়ে ভাঙলেম। যা ভেবেছিলেম তা হল না, শুধু লজ্জা পেলেম।
তার পরে সেদিন রাসযাত্রা।
মধুবনে জ্যোৎস্নারাতে তাঁবু পড়ল। সমস্ত রাত নাচ হল, গান হল।
পরদিন সকালে হাতির উপর হাওদা চড়ল। পর্দার আড়ালে বসে ঘরে ফিরছি, এমন সময় দেখি, বনের পথ দিয়ে কে চলেছে, তার নবীন বয়েস। চূড়ায় তার বনফুলের মালা। হাতে তার ডালি; তাতে শালুক ফুল, তাতে বনের ফল, তাতে খেতের শাখ।
ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, ‘কোন্ ভাগ্যবতীর ছেলে পথ আলো করেছে।’
ছত্রধারিণী বললে, ‘জান না? ঐ তো দুয়োরানীর ছেলে। ওর মার জন্য নিয়ে চলেছে শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাক।’
তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই।
রাজা এসে বললে, ‘তোমার কী হয়েছে, কী চাই।’
আমি বললেম, ‘আমার বড়ো সাধ, রোজ খাব শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাক; আমার ছেলে নিজের হাতে তুলে আনবে।’
রাজা বললে, ‘আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।’
সোনার পালঙ্কে বসে আছি, ছেলে ডালি নিয়ে এল। তার সর্বাঙ্গে ঘাম, তার মুখে রাগ। ডালি পড়ে রইল, লজ্জা পেলেম।
তার পরে আমার কী হল কী জানি।
একলা বসে থাকি, মুখে কথা নেই। রাজা রোজ এসে আমাকে শুধোয়, ‘তোমার কী হয়েছে, কী চাই।’
সুয়োরানী হয়েও কী চাই সে কথা লজ্জায় কাউকে বলতে পারি নে। তাই তোমাকে ডেকেছি, স্যাঙাৎনি। আমার শেষ কথাটি বলি তোমার কানে, ‘ঐ দুয়োরানীর দুঃখ আমি চাই।’”
স্যাঙাৎনি গালে হাত দিয়ে বললে, “কেন বলো তো।”
সুয়োরানী বললে, “ওর ঐ বাঁশের বাঁশিতে সুর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগলে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।”
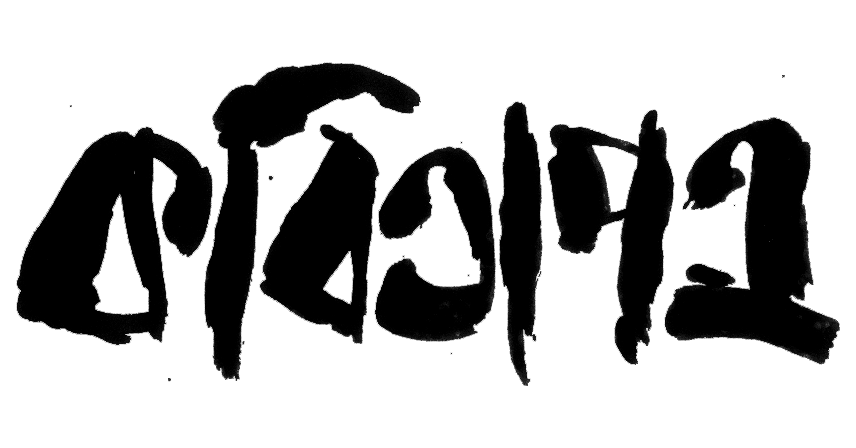
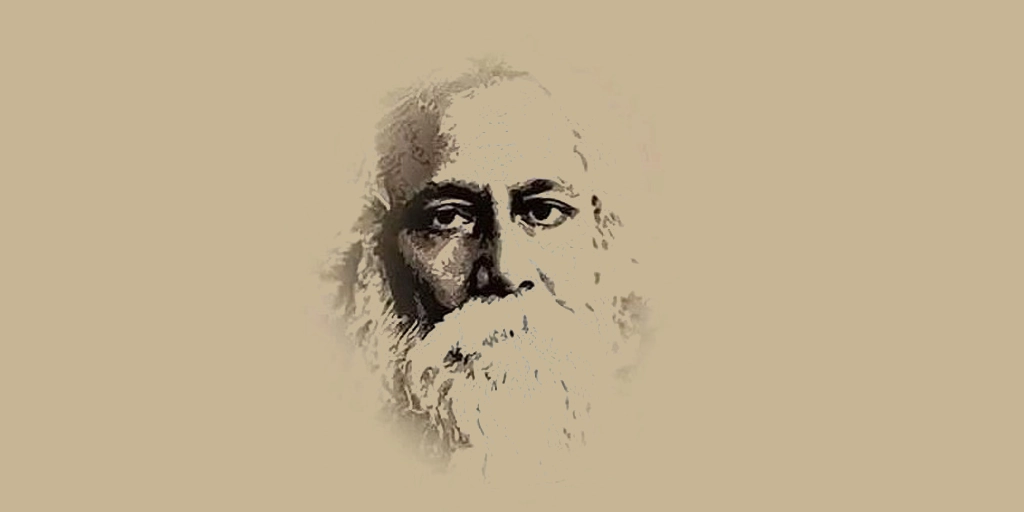





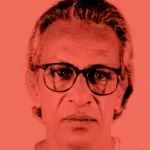
০টি মন্তব্য